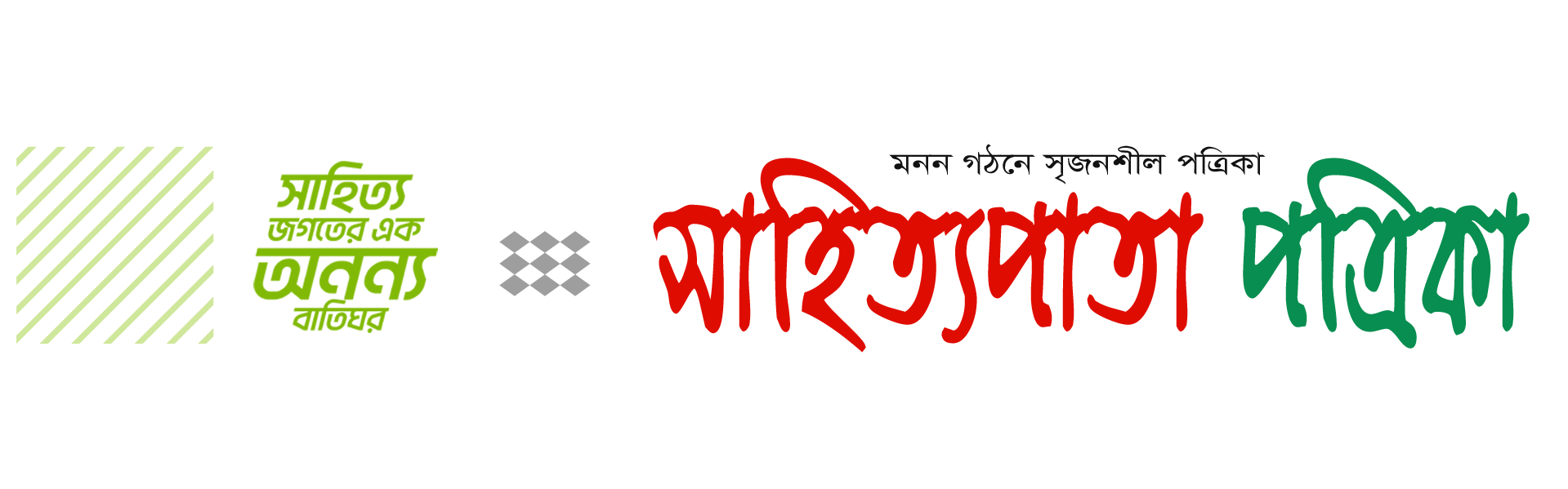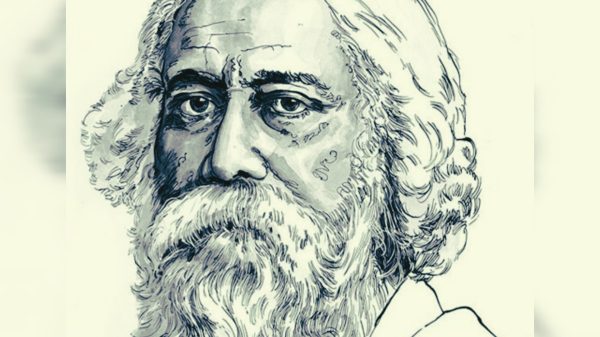‘অমর একুশে ফেব্রুয়ারির শিক্ষা ও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বাঙালি সমাজের উপর বৈষম্য || ইতাঙ্গীর খন্দকার
- সময় শুক্রবার, ২১ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫
- ৫৭১ বার দেখা হয়েছে

১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে বাঙালি সমাজের উপর যে প্রহসনমূলক অত্যাচার কিংবা অবিচার চালানো হয়েছে তার পরবর্তী ফলাফল হিসেবে ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা স্বাধীনতার অর্জন করি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল মধ্যবর্তী সময়ে ঘটে গিয়েছিল ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি তার মধ্যে অন্যতম ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। দীর্ঘ ২৪ বছরের ইতিহাসে শুধুই বাঙালি সমাজের উপর শোষণ, উৎপীড়ন, অবিচারের ইতিহাস। পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালিদের উপর পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে বৈষম্যের সৃষ্টি করে পরবর্তী ইতিহাসে তা কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে পরিচিত।
পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী আমাদের উপর যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলো তার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিলো না! উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ১৯৪৭ সালে যখন করাচীতে পাকিস্তানের রাজধানী স্হাপন করা হয় তখন এর উন্নয়ন ব্যয় ধরা হয় হয় ২০০ কোটি টাকা। পরবর্তীতে আইয়ুব খান রাজধানী ইসলামাবাদে স্থানান্তর করলে এর উন্নয়নের জন্য ব্যয় ধরা হয় ২০ কোটি টাকা অথচ দেশের দ্বিতীয় রাজধানী বলে খ্যাত ঢাকার উন্নয়নের জন্য ব্যয় ধরা হয় মাত্র ২ কোটি টাকা।
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাষাগত বৈষম্য মূলত বাংলা ভাষার প্রতি তাদের অবহেলা এবং উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়, যার দুটি অংশ ছিল—পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান) এবং পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বললেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত নেয়, যা ভাষাগত বৈষম্যের সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু চাপিয়ে দেওয়া: ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, “উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।” এটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করে। সরকারি দপ্তর, প্রশাসন, শিক্ষা এবং গণমাধ্যমে উর্দুর প্রচলন বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, অথচ তখনকার পাকিস্তানের প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলত। উচ্চশিক্ষা ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও উর্দুভাষীদের বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হতো, ফলে বাংলাভাষীরা বৈষম্যের শিকার হতো।১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে শহীদ হন। এর ফলে ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ১৯৫৬ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।এই ভাষাগত বৈষম্য পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে বঞ্চনার অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে, যা পরবর্তীতে স্বাধিকার আন্দোলন এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
ভাষা ছাড়াও এমন কোনো ক্ষেত্র ছিলো না যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বেষম্যের সৃষ্টি করেনি। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও ৭৫ শতাংশ নিয়োগ দেওয়া হতো পশ্চিম পাকিস্তানিদের। বাঙালি সমাজের উপর অর্থনৈতিক শোষণ নীতিও ছিলো উল্লেখযোগ্য — পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের ২০শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশ এ অঞ্চলের গরিব, অসহায় মানুষের জন্য বরাদ্দ ছিলো! চব্বিশ বছরের ইতিহাসে উনিশ বছরই তাদের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সেনাবাহিনীর প্রধান, বিমান বাহিনীর প্রধান, নৌবাহিনীর প্রধানসহ, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনামন্ত্রী তাদের অঞ্চলের, তাদের ঘরের, তাদের ইশারায় চব্বিশ বছরের মধ্যে চব্বিশ বছরই শাসনকার্য পরিচালনা করেন।
সমাজ কল্যাণের ক্ষেত্রেও একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ৫ কোটি ৫০ লক্ষ অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিলো ৭ কোটি ৫০ লক্ষ। এতো বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা থাকার পরেও পূর্ব পাকিস্তানের মোট ডাক্তার ছিলো ৭, ৬০০ জন মাত্র! অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের ডাক্তারের সংখ্যা ছিলো ১২,৭০০ জন । পূর্ব পাকিস্তানের মোট হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ছিলো ৬০০০ টি মাত্র! অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের হাসপাতালে বেডের সংখ্যা ছিলো মাত্র ২৬০০০ টি ! এমন কোনো ক্ষেত্র ছিলো না যেখানে বাঙালি জনসাধারণ বৈষম্যের স্বীকার হয়নি।
১৯৫২ সালে মাতৃভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিলো আমাদের ভাষা সৈনিকেরা। তারা আমাদের প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে প্রেরণার কথা বলে। অমর একুশ আমাদের শিক্ষা দেয়— ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান – একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের শেখায় যে মাতৃভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও পরিচয়ের প্রতিচ্ছবি। ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখে। একুশ আমাদের শিক্ষা দেয় —অধিকার আদায়ে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা – ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দেখিয়েছে যে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের জন্য লড়াই করলে বিজয় সম্ভব। এই শিক্ষা সমাজের সকল স্তরে ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে দাঁড়ানোর অনুপ্রেরণা দেয়। অমর একুশ আমাদের আরোও শিক্ষা দেয়— বলিদানের মূল্য ও ত্যাগের গুরুত্ব – ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগ আমাদের শেখায় যে জাতির অগ্রগতির জন্য ত্যাগ স্বীকার অপরিহার্য। সঠিক পথের জন্য আত্মত্যাগ কখনো বৃথা যায় না, বরং তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথপ্রদর্শক হয়ে থাকে।
এই শিক্ষাগুলো আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করা উচিত, যাতে আমরা আমাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ন্যায়বোধ অটুট রাখতে পারি।
ইতাঙ্গীর খন্দকার
শিক্ষার্থী,চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।